মওলানা ভাসানী ও ইসলামী সমাজতন্ত্র

ভাসানী সমাজতন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু শেষ দিকে তিনি ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলছিলেন। এ নিয়ে বিস্ময় ও হতাশা দু'টোই দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে তাঁর অনুরাগী ও অনুসারীদের ভেতরে। বদরুদ্দীন উমর মনে করেন যে, এটা ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের একটি মস্ত বড় পশ্চাদ্গমন। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে তিনি লিখেছেন, Whether the Maulana and his political associates understand the import of such declarations or not is a different question, but the fact of the matter is that by his latest stand the Maulana has struck at the very root of democratic politics in this country.
হ্যাঁ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য মওলানা ভাসানীর ওই অবস্থানটা অবশ্যই ক্ষতিকর হয়েছে, কিন্তু অতটা মারাত্মক নয় যতটা মনে করা হচ্ছে। প্রথমত, তার ইসলামী সমাজতন্ত্র ছিল ভুট্টোর ইসলামী সমাজতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভুট্টো আওয়াজটা তুলেছিলেন ভোট পাওয়ার জন্য; ভাসানী তুলেছেন যখন তিনি ভোটের রাজনীতি পরিত্যাগ করেছেন তখন। দ্বিতীয়ত, তিনি ইসলামের কথা বলেছেন হয়তো কৌশল হিসেবেই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি ধর্মবিরোধী এবং তার ওঠাবসা নাস্তিকদের সঙ্গে; শত্রুপক্ষ এমন হুমকিও দিচ্ছিল যে ইন্দোনেশিয়াতে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে যেভাবে কমিউনিস্টদের নিধন করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তানেও তেমন ঘটনা ঘটানো হবে।
তিনি যে ধর্মবিরোধী নন, তার প্রমাণ উপস্থিত করার একটা ব্যাপার ছিল। তৃতীয়ত, তিনি জানতেন যে, যে মেহনতিদেরকে তিনি আন্দোলনে নিয়ে আসতে চেয়েছেন তাদের অধিকাংশই মুসলমান, এবং তারা ধর্মের ভাষায় ডাক দিলে যেভাবে সাড়া দেবে অন্যকিছুতেই তেমন সাড়া দেবে না। তাদের সাংস্কৃতিক মানটা ছিল ওই পর্যায়েরই। স্মরণীয় যে ভাসানী সংস্কৃতি নিয়ে খুবই ভাবতেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের পাশাপাশি কাগমারীতে তিনি তিনদিনব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিলেন। আয়োজনটির ধরন দেখলে বোঝাই যায় সংস্কৃতির চর্চাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, চর্চাকে তিনি গ্রামে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, আবার তাকে আন্তর্জাতিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গেও সম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছেন। বস্তুত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সেটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। কাজটা করতে গিয়ে তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের তো বটেই, মার্কিনপন্থি সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী ইত্তেফাক পত্রিকা দ্বারাও ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনাধীন সময়ে তিনি যে কৃষক স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্রের 'জরুরি কথা' হিসেবে প্রথম বাক্যটিই ছিল সংস্কৃতি বিষয়ক। সেটি ছিল এই রকমের: 'মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব মানুষকে লইয়া মানুষের জন্যই অনুষ্ঠিত হইবে।' তাতে বলা হয়েছিল এই মানুষ হচ্ছে 'দেশের জনসাধারণ যারা শোষিত ও নিগৃহীত হচ্ছে'। আরও বলা হয়, 'এই শোষণের অবসান ঘটাইয়া সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা কায়েম করিবার প্রাথমিক স্তর হিসেবে দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন।'
বলা হয়েছিল যে, এই বিপ্লব কোনোমতেই সংস্কারমূলক হবে না; এর লক্ষ্য হবে 'সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণহীন, মহান সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। এই লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা চলিতে থাকিবে।' এর জন্য যা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হবে তা হলো কৃষক সমাজকে ভালোভাবে বোঝানো যে, 'কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থাই তাহাদের সকল দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ-অবসান ঘটাইবে- অন্যকোনো ব্যবস্থাই কৃষক জীবনে উন্নয়ন ও প্রাচুর্যের ছোঁয়াচ আনিতে পারিবে না।'
সাংস্কৃতিক মানের নিম্নস্তরবর্তিতাকে মেনে নিয়ে এবং সেটিকে উন্নত করবার জন্য কৃষকদের কাছে পৌঁছবার উপায় হিসেবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 'ইসলাম' যোগ করাকে হয়তো কার্যকর পন্থা বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সমাজতন্ত্রে যে হিন্দু মুসলমান নাই, সেটি যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ইহজাগতিক ব্যবস্থা সেটা তিনি জানতেন না এমনটা মনে করবার কারণ নেই। ভাসানীর প্রস্তাবের, এবং অনড় অবস্থানের কারণেই কৃষক সমিতির লক্ষ্য হিসেবে 'সমাজতন্ত্র' কথাটা যুক্ত হয়। রুশপন্থিরা আপত্তি করেছিলেন, তাদের ধারণা ঘোষণাপত্রে সমাজতন্ত্র থাকলে সমিতির গণচরিত্র নষ্ট হবে।
এ সময়ে অভিযোগ উঠেছিল যে মওলানা ভাসানী সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছেন। অথচ মওলানার পক্ষে আর যাই হোক না কেন, সাম্প্রদায়িক হওয়াটা ছিল একেবারেই অসম্ভব। এর সাক্ষ্য তাঁর সারাজীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম। বলিষ্ঠ সাক্ষ্য দিচ্ছেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ। হাজী দানেশ ও মওলানা ভাসানী এক সময়ে একইসঙ্গে ছিলেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। ১৯৫০ সালে মওলানার বয়স তখন ৭০; হাজী দানেশের বয়স ৫০। মওলানা জেলে গেছেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে; হাজী দানেশের কারাভোগ গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার দায়ে। হাজী দানেশ লিখছেন, '৫০ সালের সেই পরিচয় থেকে আমি দেখেছি মওলানা সাহেবের মতো অসাম্প্রদায়িক কোনো ব্যক্তি নেই।'
আর সমাজতন্ত্রে মওলানার অঙ্গীকার কতটা যে দৃঢ় ছিল তার সাক্ষ্যও হাজী দানেশ দিয়েছেন। মৃত্যুর ২ বছর আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, মওলানা ভাসানী 'আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাইতেন। নিপীড়িত মানুষের একদিন মুক্তি আসবে, আর তা একমাত্র কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে আসবে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি কমিউনিস্টদের ভালোবাসতেন। শ্রদ্ধা করতেন।'
আইয়ুবের পতনের পরে নতুন করে সামরিক শাসন যখন জারি হলো রাজনৈতিক নেতারা তখন হতভম্ব; কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ভাসানীর উদ্ভাবিত ঘেরাও অনেকটা সফল হয়েছে; কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে 'ঘেরাও' চলবে না বোঝা যাচ্ছিল। ভাসানী তখন উদ্ভাবন করেন কৃষক সম্মেলন। প্রথমে অনুষ্ঠান করেন পাকশিতে, অক্টোবর ১৯৬৯ সালে। সেটা ছিল পরীক্ষামূলক। তারপরে বড় আকারে করেন শাহপুরে। ঘরোয়া রাজনীতির তখন অনুমোদন ছিল। সম্মেলনের মাঠে বাঁশের বেড়া ও লাল কাপড়ের ঘের তৈরি করে সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন, এটা প্রকাশ্য নয়, ঘরোয়া বৈঠক বটে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কৃষকবাহিনী গঠন করা; বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন কৃষক স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী; এই সময়ে লালটুপির উদ্ভাবনও তিনিই ঘটালেন। লালটুপির পেছনে ছিল চীন ও রুশ বিপ্লবের রেড গার্ডদের স্মৃতি।
তারপরে জানুয়ারিতে যখন প্রকাশ্য রাজনীতি করার ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হলো, তখন একের পর এক সম্মেলন হলো সন্তোষে, মহীপুরে, ঢাকায়, খুলনায়, ময়মনসিংহে। এমনকি ১৯৬৯ সালের ২ অক্টোবর ঢাকায় যেদিন ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ বৈঠকটি হয় সেদিন সকালেও রেসকোর্স ময়দানে কৃষক শ্রমিক সমাবেশ ও লালটুপি মিছিল করা হয়েছিল। কারো কারো ধারণা, লাখখানেক লোক উপস্থিত ছিল। প্রতিটি কৃষক সম্মেলনেই তিনি সমাজতন্ত্রের আবশ্যকতার কথা খুব জোর দিয়ে বলতেন।
১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানে যান, সেখানকার ন্যাপের এবং হারি (কৃষক) সমিতির আহ্বানে। ওই সফরে যে সমস্ত জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন তাতে তার বক্তব্য মোটেই ধর্মবিষয়ক ছিল না, ছিল সামাজিক বিপ্লব বিষয়ক। তিনি বলেছিলেন পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুদেরকে জনসাধারণের দাবিদাওয়া মেনে নিতে হবে। বলেছিলেন পাকিস্তানি সরকার আন্দোলনের সময় যত মানুষকে খুন করেছে ব্রিটিশ শাসনের আমলে ততো করা হয়নি।
খুব বড় আকারে একটি কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল পাঞ্জাবের টোবাটেক সিং নামের একটি প্রান্তিক এলাকাতে। সম্মেলনটি ছিল যাকে বলে ঐতিহাসিক। এতে যেমন যোগ দিয়েছিলেন লাহোরের আরিফ ইফতেখারউদ্দিন ও মুলতানের কিশওয়ার গারদেজির মতো বিত্তবানরা, তেমনি এসেছিলেন হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক; এসেছিলেন কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে; এসেছিলেন করাচির শ্রমিকনেত্রী কানিজ ফাতিমা। সম্মেলনের দৃশ্যাবলী ও ঘটনাপ্রবাহ কেমন ছিল তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় লাহোরের এক সাংবাদিকের বর্ণনায়; উর্দু ভাষায় লিখিত একটি পুস্তকে তিনি জানাচ্ছেন : 'মওলানা ভাসানীকে নিয়ে গাড়ি টোবাটেক সিং-এ পৌঁছুলে চারদিকে দেখা যায় শুধু লালটুপি। ঢোল, বাদ্য, স্লোগান সহকারে তারা মওলানাকে স্বাগত জানায়। জনতার সমুদ্রে কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছিল না। সবাই নিজেই স্লোগান দিচ্ছিল আবার নিজেই জবাব দিচ্ছিল। সবাই বিপুল উদ্দীপনায় মওলানার কথা শোনার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। রেলস্টেশন থেকে মওলানাকে মিছিল করে শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। শিশুরা আনন্দে নৃত্য করছিল। চাদর এবং দোপাট্টা গায়ে মেয়েরা মওলানার উপর এবং মিছিলের উপর ফুল বর্ষণ করে আনন্দ প্রকাশ করছিল। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। যুবকদের স্লোগান দিতে দিতে গলা বসে গিয়েছিল। সম্মেলনের অদূরে মেলা বসেছিল। রকমারী দোকানপাট সাজিয়ে স্বল্পমূল্যে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের দোকানীরা খাবার সরবরাহ করছিল। এক আনা মূল্যের একটি রুটি খেলে পেট ভরে যেতো। তাও রুটির সঙ্গে তরকারি বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছিল। রহিমইয়ার খান, বাহাওয়ালপুর, লাহোর, ওহাড়ি, ভাওয়ালনগর, কবিরওয়ালা, বুরেওয়ালা, সারগোদা, লুধহারান, ঝং, ডেরাগাজী খান, শিয়ালকোট, হাজরা, রাওয়ালপিন্ডি, ক্যাম্বেলপুর, গুজরাট, গুজরানওয়ালা, কিলাস, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, মর্দান, সোয়াত, কোর্ট সেন্টিমেন, কোয়েটা, লাসবেলা এবং করাচি থেকে শ্রমিকরা সম্মেলন স্থলে এসে সমবেত হয়। মোদ্দা কথা "সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান" যেন টোবাটেক সিং-এ ভেঙে পড়েছিল। চারদিক থেকে লোকারণ্য। মেয়েদের প্রতি কেউ চোখ তুলে তাকাচ্ছিল না। যেন ভাই-বোন সবাই একত্রিত হয়েছে।'
ভাসানীর আহ্বানটি ছিল সমাজতান্ত্রিক। পূর্বে যেমন পশ্চিমেও তেমন। কথিত ইসলামী সমাজতন্ত্রের আওয়াজ তোলার আরও একটি কারণ হতে পারে ক্ষোভ ও অভিমান। মওলানাকে ছেড়ে তার অনুসারীরা একে একে চলে গেছেন। সবশেষে গেছেন চীনপন্থি কমিউনিস্টরা। এঁদের চলে যাওয়াতে তিনি কত যে মনোকষ্ট পেয়েছিলেন ১৯৬৭ সালে ন্যাপের রংপুর সম্মেলন তাঁর বক্তৃতাতে তার একটি প্রকাশ ঘটেছিল। ওই বক্তৃতাতে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বলেছেন, 'আমি সিলেট রেফারেন্ডামে পাকিস্তানের জন্য লড়েছি, কিন্তু পাকিস্তান হবার পর জিন্নাহ সাহেব প্রথম গ্রেফতার করেন আমাকে। দুঃখ তখন পাইনি। আমি যখন রংপুরে আসি আমার স্নেহাস্পদ মশিউর রহমান যাদু মিয়া এক গাড়ি লোক পাঠিয়ে দিয়ে স্লোগান দিল, "ভাসানী ফিরে যাও"। দুঃখ তখনও পাইনি। যে আওয়ামী লীগ নিজে হাতে গড়লাম, সেই আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, যে মুজিবকে স্নেহ করতাম সেই মুজিবও বিরুদ্ধে গেল। দুঃখ তখনও পাইনি। কিন্তু যারা আমাকে কাটমোল্লা থেকে সমাজতন্ত্রী বানাল, সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত করলো, নতুন করে আমার জন্ম দিল, তারা যখন কুৎসা করে তখন তো আর দুঃখ ধরে রাখতে পারি না।' হায়দার আকবর খান রনো ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তার মনে আছে ভাসানীর সেই বক্তৃতাতে শ্রোতাদের অনেকেই কেঁদেছিলেন।
ভাসানী যখন কৃষক সম্মেলন করছেন দলত্যাগ তখনও ঘটেছে। সাহিত্যিক আবদুল হক তার ২৮ জুন ১৯৭০-এর দিনলিপিতে লিখেছেন : 'ভাসানী ন্যাপে ভাঙন। গত কয়েক মাসে ভাসানী ন্যাপের এইটিই সবচেয়ে বড়ো কথা। জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ তোয়াহা পদত্যাগ করেছেন মাস দু'য়েক আগে।' হয়তো কোনো একটা নয়, ওপরে উল্লেখিত সবক'টি কারণই একত্রে মিলেছিল মওলানাকে 'পশ্চাদপসরণে' বাধ্য করতে। 'পশ্চাদপসরণ' যতটাই হোক না কেন, সমাজতন্ত্রে নিজের আস্থাকে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর ভরসার ব্যাপারটাকে তিনি কখনোই দূরে সরিয়ে দেননি।








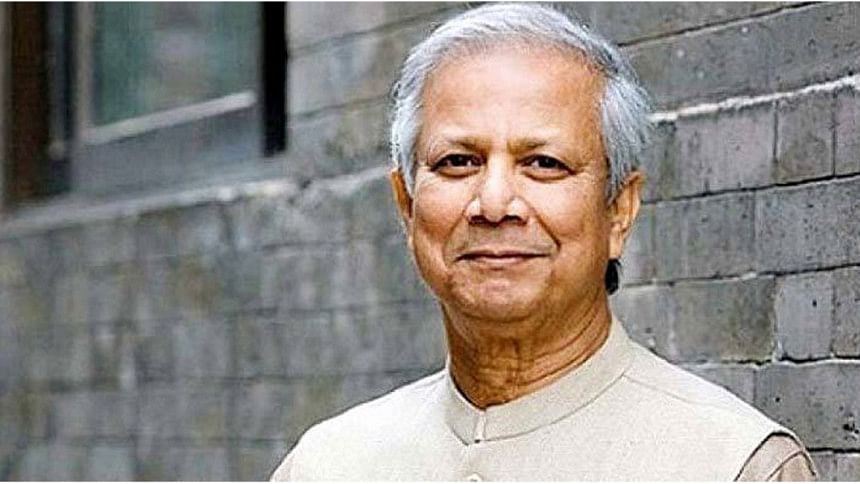













Comments